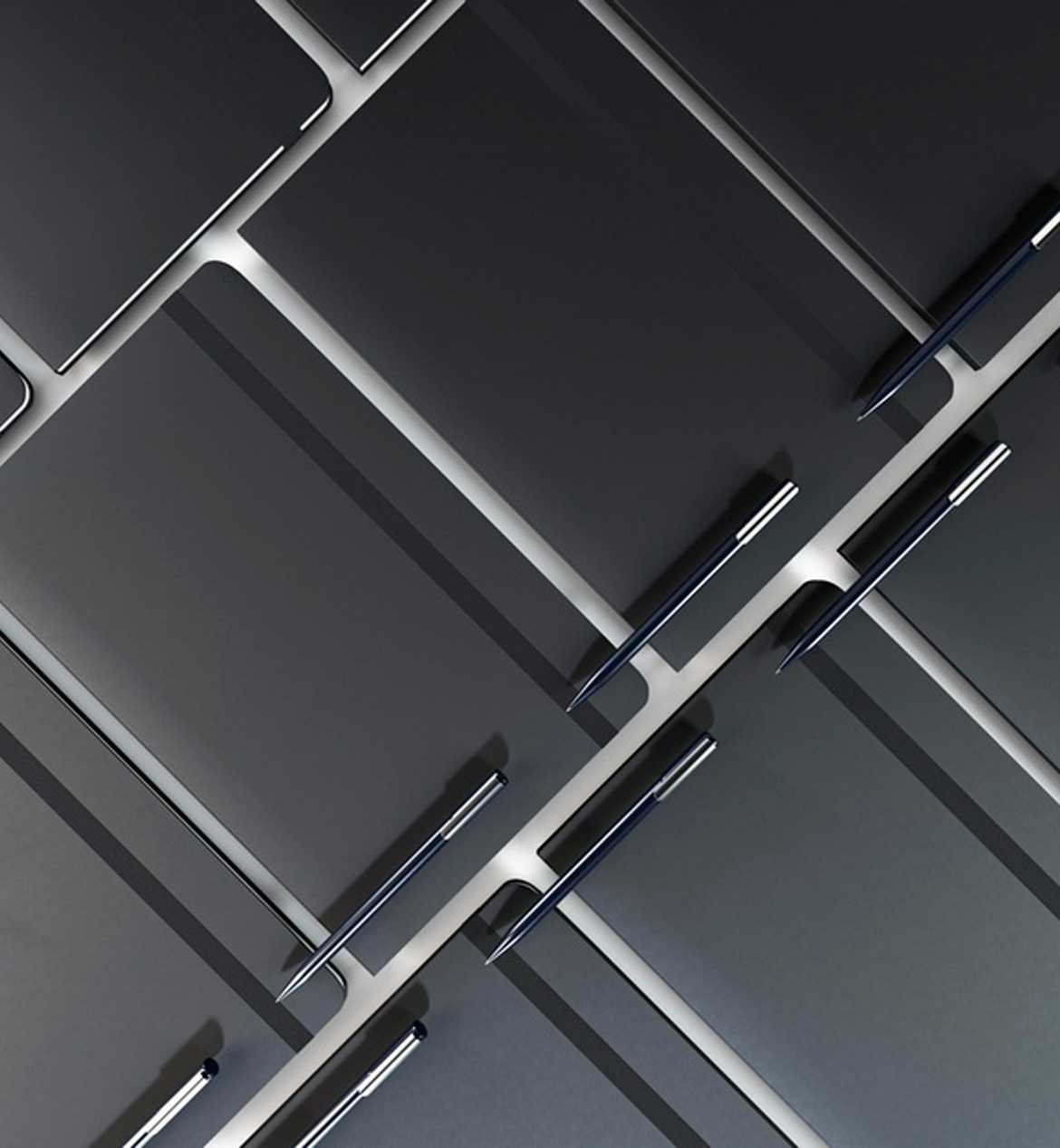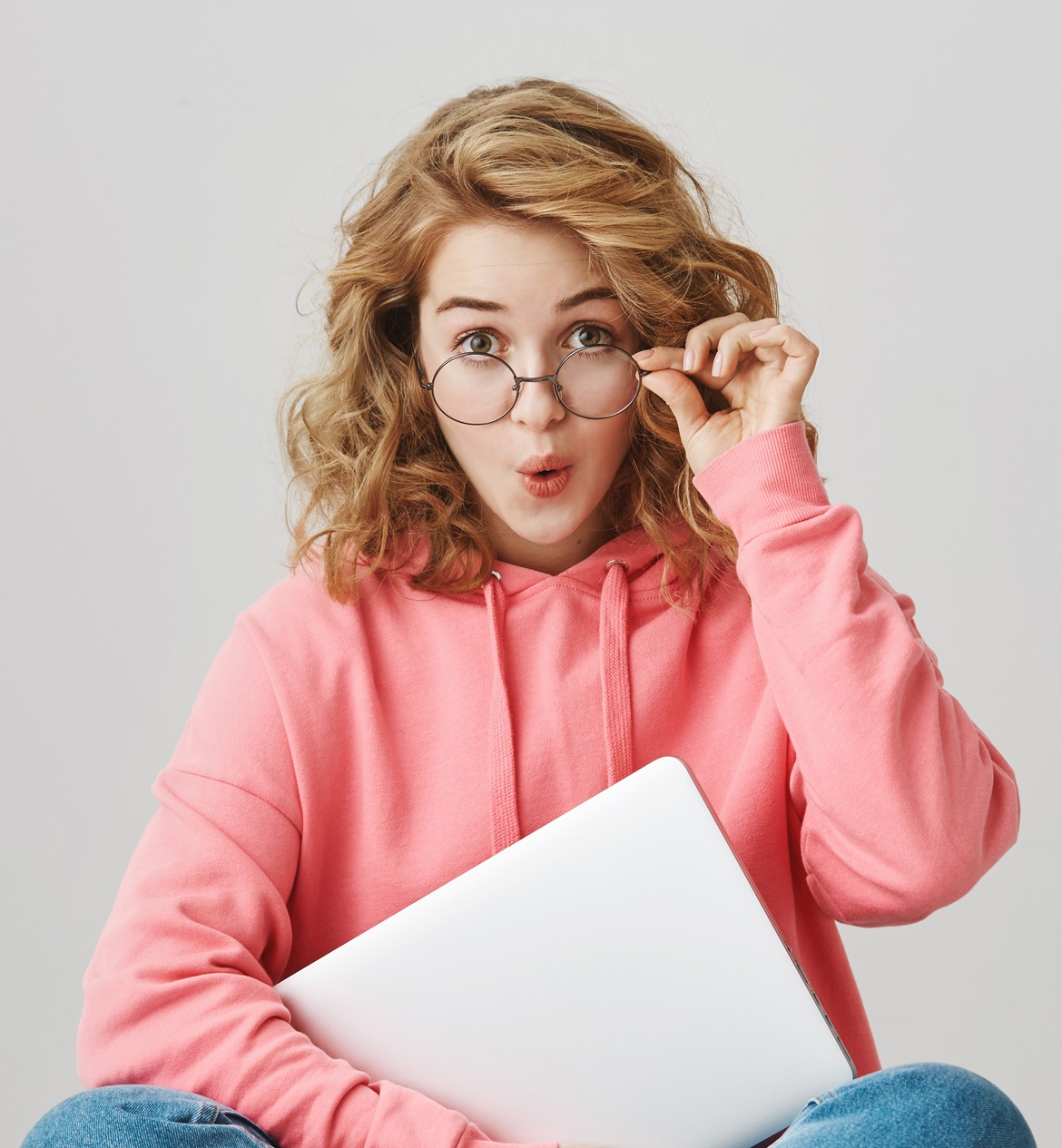THE SUN MOVES AROUND THE EARTH সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি নেই?
বিজ্ঞানের পরিভাষায় পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে প্রধানত:দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে। উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিভ্রমণকালে পৃথিবী নিজ কক্ষতলের উপর সর্বদা ৬৬.৫ ডিগ্রী কোণে হেলে স্থান পরিবর্তন করছে। বিজ্ঞানের এ ধারণা সঠিক হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অনুসারে হেলে থাকা পৃথিবীর উপরদিকে অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর মেরু বা উত্তর গোলার্ধ নদী-নালা খাল-বিল বিহীন এক কথায় পানিশূণ্য থাকবে। যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম হচ্ছে উপরের দিকের বস্তু নিচের দিকে পতিত হওয়া। কিন্তু পৃথিবীর উত্তর মেরু বা উত্তর গোলার্ধতো পানি শূণ্য নয় বরং পানিতে ভরপুর। অপরদিকে বিজ্ঞানের ধারণা মতে পৃথিবী বার্ষিক গতির সময় ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবী ক্রমশ:উত্তর দিকে হেলতে থাকে। বিজ্ঞানের এ ধারণা সঠিক হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে বা উত্তর গোলার্ধে ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস একটানা জোয়ার হতে থাকবে। আবার বিজ্ঞানের ধারণা মতে পৃথিবী বার্ষিক গতির কারণে ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত পৃথিবী ক্রমশ:দক্ষিণ দিকে হেলতে থাকে। বিজ্ঞানের এ ধারণাও সঠিক হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর উত্তর মেরু বা উত্তর গোলার্ধে ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত একটানা ছয় মাস ভাটা হতে থাকবে। কিন্তু আদৌ পৃথিবীতে কোথাও একটানা ছয় মাস জোয়ার এবং একটানা ছয় মাস ভাটা হয় না। তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি ভুল?
বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র কি ভুল?
বিজ্ঞানের ধারানায় প্রত্যেকটি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। যে জন্য প্রত্যেকটি গ্রহ বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় আপন অক্ষের উপরও ঘুরছে। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রহ যেমনি দূরত্বের ব্যবধানে সামঞ্জ্যপূর্ণতার সঙ্গে বা ধারাবাহিকতার সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তেমনি সামঞ্জ্যপূর্ণতার সঙ্গে বা ধারাবাহিকতার সঙ্গে আপন অক্ষের উপরও ঘুরছে না কেন? যেমন পৃথিবী ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে কিন্তু বুধগ্রহ সূর্যের একেবারে নিকটবর্তী গ্রহ হওয়া সত্ত্বেও ৫৯ দিনে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। আবার বৃহস্পতি গ্রহ সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করেও মাত্র ৯ ঘন্টা ৫৫ মিনিটে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান যেমনি পৃথিবী ৩৬৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে তার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় আপন অক্ষের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরছে বলে ধারণা করছে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান চন্দ্রকে ২৭.৩৩ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করার কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া কি তা উল্লেখ করেনি। আবার বিজ্ঞান সূর্যকে আপন অক্ষের উপর ২৫ দিনে একবার ঘুরছে বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু তার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া কি তা উল্লেখ করেনি। তাহলে বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি কি ভুল?
বাস্তবক্ষেত্রেও কি ভুল?
বিজ্ঞানের ধারণায় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে সূর্যকে গ্রীস্মকালে অর্থাৎ ২১ জুন উত্তর দিকে দেখা যায় এবং শীতকালে অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিকে দেখা যায়। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে শীত-গ্রীস্মে শুধুমাত্র সূর্যকে ছাড়া অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রকে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? শীত-গ্রীস্ম সব সময় সকল গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একই বরাবর দেখা যায় কেন? বাস্তবক্ষেত্রে তো চন্দ্রকে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে এবং শীতকালে উত্তর দিকে দেখা যায়। অথচ বিজ্ঞানের ধারণায় গ্রীষ্মকালে সূর্যকে যে বরাবর দেখা যায় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে শীতকালে তার চেয়ে দক্ষিণ দিকে দেখা যায়। বিজ্ঞানের এ ধারণা সঠিক হলে সূর্যের মতই চন্দ্রকে গ্রীষ্মকালে যে বরাবর দেখা যায় শীত কালে তার চেয়ে দক্ষিণ দিকে দেখা যাওয়ার কথা। ঠিক এমনিভাবে বাস্তবক্ষেত্রে চন্দ্রকে শীতকালে যে বরাবর দেখা যায় বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে গ্রীষ্মকালে চন্দ্রকে আরও উত্তর দিকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে চন্দ্রকে গ্রীষ্মকালে যে বরাবর দেখা যায় শীতকালে দক্ষিণ দিকে দূরের কথা বরং চন্দ্রকে শীতকালে যে বরাবর দেখা যায় গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকের পরিবর্তে আরও দক্ষিণ দিকে দেখা যায়। তাহলে বিজ্ঞানের ধারণা মোতাবেক বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে সূর্যকে যেমনি শীতকালে দক্ষিণ দিকে আর গ্রীষ্মকালে উত্তরদিকে দেখা যায় তেমনি চন্দ্রকেও একই তুলনায় শীত-গ্রীষ্মে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? বরং শীত-গ্রীষ্মে চন্দ্রকে বিপরীত দিকে দেখা যায় কেন? পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের ধারণা মোতাবেক বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে সূর্যকে যেমনি শীতকালে দক্ষিণ দিকে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে দেখা যায় তেমনি আকাশের শত কোটি নক্ষত্র সহ কোন্ গ্রহটি পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে শীতকালে যে বরাবর দেখা যায় গ্রীষ্মকালে তার চেয়ে উত্তর দিকে দেখা যায়? অথবা গ্রীষ্মকালে যে বরাবর দেখা যায় শীতকালে তার চেয়ে দক্ষিণ দিকে দেখা যায়? প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র সূর্য ছাড়া আকাশের কোন গ্রহ-নক্ষত্রকে শীতকালে দক্ষিণ দিকে আর গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে দেখা যায় না বরং শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্রকে একই বরাবর দেখা যায়। তাহলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে আকাশের সকল গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া কি শুধুমাত্র সূর্যকে শীতকালে দক্ষিণ দিকে আর গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে দেখা যাবে?
পক্ষান্তরে অনেক সময় রাতে আকাশ কখনো উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে, আবার কখনো দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে, আবার কখনো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দ্রুত গতিতে নক্ষত্র চলতে দেখা যায়। বিজ্ঞাণের ভাষায় তাকে কক্ষচ্যুত নক্ষত্র বলা হয়। মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিটের ভিতর এসব নক্ষত্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করে। তাহলে সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড় এবং সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি কি. মি. দূরের এসব কক্ষচ্যুত নক্ষত্র মাত্র ১০ মিনিটের ভিতর আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হলে দীর্ঘ ২৪ (চবিবশ) ঘন্টায় আকাশের প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে অতিক্রম করতে পারবে না কেন?
প্রকাশিত- দৈনিক রানার, যশোর। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ইং।
The Daily News Today-Dhaka. 22 Nov. 2011.
দৈনিক দিনকাল-ঢাকা। ৯ই আগষ্ট-২০১২ইং।
সূর্য আকর্ষণহীন !
বিজ্ঞানের ধারণা সূর্যের প্রবল আকর্ষণে বিশাল বিশাল ভারী গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীও নাকি একটি গ্রহ। পৃথিবী নাকি তার উপগ্রহ চন্দ্রকে নিয়ে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য এক বিশাল অগ্নিপিন্ড। তাহলে আগুনেরও কি আকর্ষণ ক্ষমতা আছে? ধাতব পদার্থ ছাড়া কি স্থায়ী চৌম্বকত্ব বা আকর্ষণ ক্ষমতা সম্ভব? সূর্যের যে প্রবল আকর্ষণে পৃথিবী বর্তমান অবস্থানে অবস্থান করছে চন্দ্র প্রত্যেক মাসে অমাবস্যার দিন ঐ প্রবল আকর্ষণের মধ্যে পতিত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের প্রবল আকর্ষণকে উপেক্ষা করে অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকে সূর্য থেকে ক্রমশ: দূরে সরায়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে সূর্যের যে প্রবল আকর্ষণ পৃথিবীকে নিজের চারিদিকে ঘোরাচ্ছে সূর্যের সে আকর্ষণ অমাবস্যার সময় চন্দ্রকে পৃথিবীর নিকট থেকে বিচ্ছন্ন পূর্বক নিজের চারিদিকে ঘোরাচ্ছে না কেন? সত্যিই যদি পৃথিবী চন্দ্রকে নিজের চারিদিকে ঘোরায় তবে অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত যেতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তার চেয়ে দ্রুত এবং কম সময় লাগবে পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত যেতে। কেননা অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ শক্তির বিপরীতে যেতে থাকে। আর পূর্ণিমার পর থেকে অমাবশ্যা পর্যন্ত চন্দ্র সূর্যের আকর্শষণ শক্তি অভিমুখে যেতে থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চন্দ্রের গতিবেগ আদৌও কি কখনো হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে? অবশ্য বিজ্ঞানের ধারণা মোতাবেক সূর্য এ বিশাল পৃথিবীকে আকর্ষণ করে রাখলে চন্দ্র পৃথিবীর দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রদক্ষিণ করলে সূর্যের আকর্ষণ শক্তি সহজে প্রমানিত হতো। কিন্তু বিজ্ঞানতো পৃথিবীকে ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরবার স্বপ্ন দেখছে। যে জন্য কল্পিত সূর্যের প্রচন্ড আকর্ষণ ক্ষমতাকে ভুলে গিয়ে নির্বিঘ্নে চন্দ্রকেও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ২৭.৩ দিনে একবার ঘোরাতে সক্ষম হচ্ছে।
চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ নয়
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ নয়। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। সে জন্য চন্দ্র ২৭.৩ দিনে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানের এ তথ্য সঠিক হলে পৃথিবী হতে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করতে গতিবেগ হ্রাস-বৃদ্ধি নিস্প্রয়োজন বরং চন্দ্র হতে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশের সময় অবশ্যই গতিবেগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ গতিবেগ পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমতূল্য হতে হবে। নতুবা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। যেমন একটা গতিশীল গাড়িতে উঠতে হলে গাড়ির গতির সমতুল্য গতিসম্পন্ন না হলে গাড়িতে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অনুরূপ স্বল্প গতি সম্পন্ন চন্দ্রের কক্ষপথ থেকে অধিক গতিসম্পন্ন পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করতে অবশ্য-অবশ্যই পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমতুল্য গতি সম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করতে অতিক্রান্ত গতিবেগ দরকার হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ২.৪ কি. মি.। নতুবা চন্দ্র অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে। যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে প্রথম ১০টি চন্দ্র অভিযান। দুর্ঘটনা ঘটুক বা যাই হোক না কেন দ্রুতগামী বা গতিশীল গাড়ি থেকে স্বাভাবিক যে কোন গতিতে নামা যাবে না কেন? অর্থাৎ স্বাভাবিক যে কোন গতিতে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করা যাবে না কেন? যেহেতু পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করতে অতিক্রান্ত গতিবেগ সেকেন্ডে ২.৪ কি. মি. দরকার। সেহেতু চন্দ্রের কক্ষপথ গতিশীল স্রোতের মতই। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাথে বাস্তবের মিল নেই। অপরদিকে চন্দ্র ২৭.৩ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে বিজ্ঞানের এ তথ্যটিও সঠিক হলে নবমী-দশমীর পর হতে পূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে চন্দ্রের অন্ধকার অংশ উপরের দিকে দেখা যাবে। কিন্তু ঐ সময় চন্দ্রের অন্ধকার অংশ নিচের দিকে দেখা যায়। অনুরূপ পূর্ণিমার পর হতে ষষ্ঠী-সপ্তমী পর্যন্ত ভোরে পশ্চিমদিকে চন্দ্রের অন্ধকার অংশ উপরের দিকে দেখা যাবে। কিন্তু ঐ সময়ও চন্দ্রের অন্ধকার অংশ নিচের দিকেই দেখা যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞান বাস্তবের বিপরীত।
প্রকৃতপক্ষে স্রোতের ভাসমান বল যেমন ভাসতে ভাসতে আপন অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে (বিপরীত প্রতিক্রিয়া) ঠিক তেমনি চন্দ্রও আপন কক্ষপথে ভাসছে অর্থাৎ প্রায় ২৫ ঘন্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে এবং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ২৯দিনে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। অর্থাৎ চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ নয়।
চন্দ্র প্রায় ২৫ ঘন্টায় পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে বিধায় চন্দ্র অভিযানের সময় চন্দ্রের কক্ষপথের মধ্যে প্রবেশের জন্য পূর্ব হতে পশ্চিম মুখী হয়ে প্রবেশ করতে হচ্ছে। আর বিজ্ঞানের ধারণা মতে চন্দ্র পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ২৭.৩৩ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী হতে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশের জন্য পশ্চিম হতে পূর্বমুখী হয়ে প্রবেশ করতে হতো। এমনকি চন্দ্রের কক্ষপথের মধ্যে প্রবেশের পর পশ্চিম হতে পূর্বমুখী হয়ে চলাচল সহজ হতো কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটছে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিপরীত। বাস্তব ক্ষেত্রে চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশের পর পূর্ব হতে পশ্চিমমুখী হয়ে যাওয়া খুব সহজ কিন্তু পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে যাওয়া খুবই কঠিণ ও কষ্টকর। কেননা চন্দ্রের কক্ষপথ পূর্ব হতে পশ্চিমমুখী। ঠিক একই কারণে চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণের পর চন্দ্র পৃষ্ঠের উপর পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে চলাফেরা যত সহজভাবে চলাচল করা সম্ভব পশ্চিম হতে পূর্বদিকে তত সহজভাবে চলাচল করা সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিম হতে পূর্বমুখীতো চন্দ্রের কক্ষপথের স্রোতের বিপরীত দিক।
প্রকাশিত- সাপ্তাহিক অহরহ-ঢাকা ৭-১৩ ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৬ ইং
সূর্যের কোন গ্রহ নেই
মাত্র পাঁচশ বছর আগে থেকে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে যে, সূর্যের গ্রহ নয়টি। প্রত্যেকটি গ্রহ সূর্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে। সূর্য থেকে গ্রহ গুলোর দূরত্বের ভিন্নতা এবং প্রদক্ষিণ সময়ের ভিন্নতার কারণে প্রত্যেকটি গ্রহ প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে পৃথিবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যিই কি পৃথিবী প্রত্যেকটি গ্রহ থেকে সর্বক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে? যেমন-
বুধগ্রহ:
বিজ্ঞানের ধারণায় সূর্য থেকে বুধ গ্রহের দূরত্ব ৩৬ মিলিয়ন মাইল এবং পৃথিবীর দূরত্ব ৯৩ মিলিয়ন মাইল। বুধগ্রহ সূর্যকে ৮৭.৯৭ দিনে একবার এবং পৃথিবী ৩৬৫.২৬ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করছে। উভয়ের প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে বুধগ্রহ পৃথিবী থেকে কখনো ৯৩-৩৬=৫৭ মিলিয়ন মাইল দূরে আবার কখনো ৯৩+৩৬=১২৯ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করার কথা । পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রমনকালে সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। ৪ জুলাই সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কি.মি. এবং ৩ জানুয়ারী ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কি.মি. দূরে থাকে। দূরত্ব বাড়লে আপাতত: দৃষ্টিতে আয়তন কমে। বিধায় জুলাই মাসে অর্থাৎ গ্রীস্মকালে সূর্যকে একটু ছোট এবং ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালে সূর্যকে একটু বড় দেখায়। তাহলে বুধগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে ১২৯ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে তখন যে আকার বা আকৃতিতে দেখা যায় তার চেয়ে যখন পৃথিবী থেকে মাত্র ৫৭ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে তখন বিশাল আকৃতিতে দেখা যায় না কেন? বুধগ্রহের আকার বা আকৃতি পৃথিবী থেকে সব সময় একই রকম দেখা যায় কেন? বিজ্ঞানের ধারণা সঠিক হলে বুধগ্রহ ও পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে বুধগ্রহ কখনো ৫৭ মিলিয়ন মাইল দূরে আবার কখনো ১২৯ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করছে না কেন অথবা করবে না কেন? আবার বিজ্ঞানের কল্পনায় পৃথিবী বার্ষিক গতির সময় হেলে যাওয়ার কারনে সূর্যকে যেমন শীতকালে দক্ষিণ দিকে আর গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে দেখা যায় তেমনি বুধগ্রহকেও শীত বা গ্রীষ্মকালে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? বুধগ্রহকে সবসময় একই বরাবর দেখা যায় কেন? অপর দিকে বিজ্ঞানের ধারণায় বুধগ্রহ যেহেতু সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে সেহেতু পৃথিবী কখনই সূর্য ও বুধগ্রহের মাঝখানে অবস্থান করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ কোন দিন মাঝরাতে বুধগ্রহকে মধ্যআকাশে দেখা যাবে না । সত্যইকি বুধগ্রহকে কোনদিন মাঝরাতে মধ্য আকাশে দেখা যায় না?
শুক্রগ্রহ:
বিজ্ঞানের ধারণায় সূর্য থেকে শুক্রগ্রহের দূরত্ব ৬৭.২ মিলিয়ন মাইল এবং ২২৪.৭ দিনে গ্রহটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তাহলে পৃথিবী এবং শুক্রগ্রহ উভয়ে প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে কখনো ৯৩-৬৭.২=২৫.৮ মিলিয়ন মাইল দূরে আবার কখনো ৯৩+৬৭.২ = ১৬০.২ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করবে। শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে ১৬০.২ মিলিয়ন মাইল দূরে অর্থাৎ সুর্যের এক পাশে পৃথিবী অপর পাশে শুক্রগ্রহ অবস্থান করবে তখন শুক্রগ্রহকে যে আকার বা আকৃতিতে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বৃহত আকার বা আকৃতিতে দেখা যাবে যখন শুক্রগ্রহ পৃথিবী থেকে মাত্র ২৫.৮ মিলিয়ন মাইল দূরে অর্থাৎ যখন শুক্রগ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝ বরাবর অবস্থান করবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শুক্রগ্রহকে কখনো ছোট বা বড় দেখা যায় না কেন? শুক্রগ্রহকে সব সময় একই আকার বা আকৃতিতে দেখা যায় কেন? বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে শুক্রগ্রহকে শীত-গ্রীস্মে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? শীত-গ্রীস্মে শুক্রগ্রহ একই বরাবর অবস্থান করে কেন? পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের ধারণা মতে যেহেতু শুক্রগ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝ বরাবর অবস্থিত সেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আদৌ কখনো পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও অপর পাশে শুক্রগৃহকে দেখা যাবে না। বাস্তবক্ষেত্রে সত্যিই কি পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও অপর পাশে শুক্রগ্রহকে দেখা যায় না? অর্থাৎ কোনদিন মধ্যরাতে কি শুক্রগ্রহকে দেখা যায় না? প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে শুক্রগ্রহ কখনো পৃথিবী থেকে ২৫.৮ মিলিয়ন মাইল দূরে আবার কখনো ১৬০.২ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করছে না কেন অথবা করবে না কেন?
মঙ্গলগ্রহ:
সূর্য থেকে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব ১৪১.৬ মিলিয়ন মাইল এবং মঙ্গলগ্রহ ৬৮৬.৯৮ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে থাকে। পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ উভয়ের প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে যখন সূর্যের একপাশে পৃথিবী ও অপর পাশে মঙ্গলগ্রহ অবস্থান করবে তখন পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব হবে ১৪১.৬+৯৩=২৩৪.৬ মিলিয়ন মাইল। কিন্তু আদৌ বাস্তব ক্ষেত্রে সূর্যের একপাশে পৃথিবী আর অপরপাশে মঙ্গলগ্রহ অবস্থান করে না কেন অথবা করবে না কেন? পক্ষান্তরে পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে যখন পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও অপরপাশে মঙ্গলগ্রহ অবস্থান করবে তখন পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব হবে ১৪১.৬-৯৩=৪৮.৬ মিলিয়ন মাইল। বিজ্ঞানের ধারণা মোতাবেক মঙ্গলগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করলে মঙ্গলগ্রহ কখনই সূর্য ও পৃথিবীর মাঝ বরাবর অবস্থান করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝ বরাবর অবস্থান করে কেন? আবার মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে যখন মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী থেকে ২৩৪.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করবে তখন যে আকার আকৃতিতে দেখা যাবে তার চেয়ে বিশাল আকৃতিতে দেখা যাবে যখন মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী থেকে মাত্র ৪৮.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ যখন মধ্যরাতে আকাশের মাঝখান বরাবর অবস্থান করে তখন বিশাল আকৃতিতে দেখা যায় না কেন? আবার শীত-গ্রীস্মে পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারনে মঙ্গল গ্রহকে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? মঙ্গলগ্রহকে সব সময় একই বরাবর দেখা যায় কেন? পক্ষান্তরে প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহ সর্বনিম্ন ২৫.৮ মিলিয়ন মাইল এবং মঙ্গলগ্রহ সর্বনিম্ন ৪৮.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করলে মঙ্গলগ্রহকে কেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ বলা হয়? শুক্রগ্রহ কেন পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হবে না?
বৃহস্পতিগ্রহ:
সূর্য থেকে বৃহস্পতি গ্রহের দূরত্ব ৪৮৩.৬ মিলিয়ন মাইল এবং গ্রহটি সূর্যকে ১১.৮৬ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। তাহলে পৃথিবী ও বৃহস্পতিগ্রহ প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে বৃহস্পতিগ্রহ কখনো ৪৮৩.৬-৯৩=৩৯০.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে আবার কখনো ৪৮৩.৬+৯৩=৫৭৬.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে না কেন অথবা করবে না কেন? আবার পৃথিবী থেকে বৃহস্পতিগ্রহ যখন ৫৭৬.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে তখন যে আকার-আকৃতিতে দেখা যায় তার চেয়ে আরও অধিক বৃহৎ আকার-আকৃতিতে দেখা যাবে যখন বৃহস্পতিগ্রহ পৃথিবী থেকে ৩৯০.৬ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আদৌও কখনো বৃহস্পতিগ্রহকে ছোট বা বড় আকৃতিতে দেখা যায় না কেন? সব সময় একই আকৃতিতে দেখা যায় কেন? আবার পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারনেও বৃহস্পতিগ্রহকে শীত গ্রীস্মে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন? সব সময় একই বরাবর দেখা যায় কেন?
শনিগ্রহ:
সূর্য থেকে শনি গ্রহের দূরত্ব ৮৮৮.২ মিলিয়ন মাইল। গ্রহটি ২৯.৪৬ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তাহলে বাস্তবক্ষেত্রে পৃথিবী ও শনিগ্রহ প্রদক্ষিণ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে শনিগ্রহ কখনো ৮৮৮.২+৯৩=৯৮১.২ মিলিন মাইল দূরে আবার কখনো ৮৮৮.২-৯৩=৭৯৫.২ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে না কেন? অথবা করবে না কেন? শনিগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে ৭৯৫.২ মিলিয়ন মাইল দূরে থাকে যখন পৃথিবী থেকে ৭৯৫.২ মিলিয়ন মাইল দূরে থাকে যখন অতি বৃহৎ আবার যখন ৯৮১.২ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থান করে তখন অতি ক্ষুদ্র দেখা যায় না কেন? অথবা দেখা যাবে না কেন? পৃথিবীর বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে শনিগ্রহকেও সূর্যের মতই শীতকালে দক্ষিণ দিকে এবং গ্রীস্মকালে উত্তর দিকে দেখা যায় না কেন? অথবা দেখা যাবে না কেন? শীত গ্রীস্মে সব সময়ই একই বরাবর দেখা যায় কেন? প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেকটি গ্রহ সব সময়ই পৃথিবী থেকে অভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে। অথচ গ্রহগুলো যদি সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় বা ঘুরে তাহলে প্রত্যেকটি গ্রহ প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে পৃথিবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করবে। যে জন্য পৃথিবী থেকে যে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। বাস্তবক্ষেত্রে যেহেতু প্রত্যেকটি গ্রহ সব সময় পৃথিবী থেকে অভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে সেহেতু গ্রহগুলো সূর্য কেন্দ্রীক নয়, বরং বৃথিবী কেন্দ্রীক।
(প্রকাশিত- দৈনিক তথ্য-খুলনা। ২৬শে ডিসেম্বর-১৯৯৫ ইং।
বিজ্ঞান সাপ্তাহিক অহরহ-ঢাকা। ১৭-২৩ জানুয়ারী ১৯৯৬ইং)
নক্ষত্রগুলোও কি সূর্যকেন্দ্রীক?
পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। বিজ্ঞানের ধারণা মোতাবেক পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রায় প্রত্যেকটি নক্ষত্র থেকে কখনো ৩০ কোটি কি.মি দূরে আবার কখনো ৩০ কোটি কি.মি নিকটে অবস্থান করবে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণকালে যখন যে নক্ষত্র থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে যেতে থাকবে তখন সে নক্ষত্রকে ক্রমশ: ছোট দেখা যাবে। আবার পৃথিবী যখন ক্রমান্বয়ে যে নক্ষত্রের নিকটবর্তী হতে থাকবে তখন সে নক্ষত্রকে ক্রমশ: বৃহৎ অতিবৃহৎ দেখা যাবে। পৃথিবী প্রতি মুহুর্তে কোন কোন নক্ষত্র থেকে দূরে আবার কোন কোন নক্ষত্রের নিকটবর্তী হওয়ার কথা। যেজন্য পৃথিবী থেকে অসংখ্য নক্ষত্রকে ক্রমশ: ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আবার অসংখ্য নক্ষত্রকে ক্রমশ: বৃহৎ হতে অতিবৃহৎ দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটা নক্ষত্রকেও আদৌ কখনো ছোট বা বড় দেখা যায় না কেন? অথবা দেখা যাবে না কেন? সারা বছরই প্রত্যেকটি নক্ষত্রকে একই আকার বা আকৃতিতে দেখা যায় কেন? যেমন- সপ্তর্ষী মন্ডল (সাত তাঁরা) ও কাসিওপিয়া (তিন তাঁরা) নক্ষত্র গোটা বিশ্ববাসীর খুবই পরিচিত নক্ষত্র। বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ কালে যখন সূর্যের একপাশে পৃথিবী আর অপর পাশে সপ্তর্ষীমন্ডল বা কাসিওপিয়া নক্ষত্র অবস্থান করবে তখন যে দূরত্বের ব্যবধানে থাকবে তার চেয়ে ৩০ কোটি কি.মি অধিক নিকটবর্তী অবস্থান করবে যখন পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও অপরপাশে সপ্তর্ষীমন্ডল বা কাসিওপিয়া নক্ষত্র থাকবে। অর্থাৎ ছয় মাস যাবত সপ্তর্ষীমন্ডল বা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রকে ক্রমশ: ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বা ছোট থেকে ছোট দেখা যাবে আবার ছয়মাস যাবত একটানা ক্রমশ: বৃহৎ হতে অতিবৃহৎ দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের কেহ কি কোনদিন সপ্তর্ষীমন্ডল অথবা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রকে বিন্দুমাত্র ছোট বা বড় দেখেছেন? সারা বছর একই আকার বা আকৃতিতে দেখা যায় কেন? পৃথিবী হেলে যাওয়ার কারণে সুর্যকে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা গেলে সপ্তর্ষীমন্ডল বা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রকেও উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দেখা যায় না কেন অথবা দেখা যাবে না কেন? আকাশের কোন্ নক্ষত্রটি সূর্যের মতই কখনো ছোট আবার কখনো বড়, কখনো উত্তর দিকে আবার কখনো দক্ষিণ দিকে দেখা যায়? সেকেন্ডে ৩০ কি.মি বেগে ধাবিত পৃথিবী আকাশের কোন্ নক্ষত্র থেকে প্রতি মুহুর্তে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে? পক্ষান্তরে পৃথিবীর উত্তর মেরু বরাবর একটা নক্ষত্রকে (ধ্রুবতারা) সব সময় একই স্থানে দেখা যায়। তাহলে বিজ্ঞানের ধারণা মতে পৃথিবী বার্ষিকগতির সময় শীতকালে ৪৭ ডিগ্রী উত্তর দিকে হেলে যাওয়ার কারণে ধ্রুবতাঁরাকে ৪৭ ডিগ্রী উপরে দেখা যায় না কেন? অথবা যাবে না কেন? আবার পৃথিবী গ্রীস্মকালে ৪৭ ডিগ্রী অধিক দক্ষিণ দিকে হেলে যাওয়ার কারণে ধ্রুবতাঁরাকে ৪৭ ডিগ্রী নীচের দিকে দেখা যায় না কেন? অথবা যাবে না কেন? তাহলে পৃথিবী কি আকাশের সকল নক্ষত্র সহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে? প্রকৃত পক্ষে সূর্য সেকেন্ডে প্রায় ১১০০০ (এগারো হাজার) কিলোমিটার গতিতে অর্থাৎ ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে এবং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় (নিউটনের তৃতীয় সূত্র) প্রায় ২৫ দিনে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। অপরদিকে চন্দ্র প্রায় ২৫ ঘন্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ২৯ দিনে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরছে। গ্রীস্মকালে সূর্য উত্তরদিকে অবস্থান পূর্বক সবচেয়ে বেশী দূরে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বিধায় দিন লম্বা হচ্ছে এবং শীতকালে দক্ষিণ দিকে এবং নিকটে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বিধায় দিন ছোট হচ্ছে। পক্ষান্তরে শীতকালে রাত লম্বা বিধায় চন্দ্র উত্তর দিকে অবস্থান পূর্বক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এবং গ্রীষ্মকালে রাত ছোট বিধায় চন্দ্র দক্ষিণ দিকে অবস্থান পূর্বক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। কারণ গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পৃথিবীই কেন্দ্রবিন্দু।